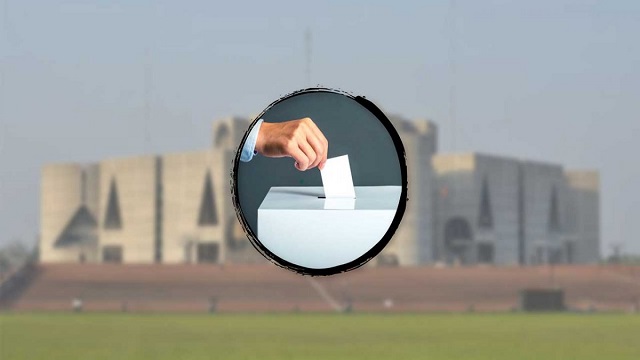
আগামী সংসদ নির্বাচন কীভাবে হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে। বিএনপিসহ কয়েকটি দল বর্তমানে প্রচলিত ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) পদ্ধতি রাখতে চায়। এই ব্রিটিশ ধারার পদ্ধতিতে প্রতিটি আসনে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী বিজয়ী হন, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া দল সরকার গঠন করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল চাইছে সংখ্যানুপাতিক বা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতি। এতে পুরো দেশকে একক আসন হিসেবে গণ্য করা হয়। ভোটাররা প্রার্থী নয়, দলীয় প্রতীকে ভোট দেন। সারাদেশে যে দল যত শতাংশ ভোট পায়, সে অনুপাতে আসন পায়। যেমন কোনো দল ১০% ভোট পেলে ৩০০ আসনের মধ্যে ৩০টি আসন পাবে। অনেক দেশে মুক্ত ও বদ্ধ উভয় ধরনের পিআর পদ্ধতি প্রচলিত।
বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা:
এফপিটিপি পদ্ধতির বড় সীমাবদ্ধতা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট সবসময় প্রতিফলিত হয় না। যেমন, কোনো আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তিনজন মিলে ৬০% ভোট পেলেও চতুর্থজন একাই ৩০% ভোট পেলে তিনিই বিজয়ী হন। যদি একইভাবে সারাদেশে ৩০% ভোট নিয়ে একটি দল জয়লাভ করে, তবে সংসদে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, অথচ ৭০% ভোটের প্রতিফলন ঘটবে না।
বাংলাদেশের অতীত উদাহরণগুলোও তাই প্রমাণ করে। যেমন ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রায় ৪৮% ভোট পেয়েছিল, কিন্তু আসন পেয়েছিল ২৩০টি—দুই-তৃতীয়াংশের বেশি। অন্যদিকে বিএনপি ৩৩% ভোট পেলেও মাত্র ৩০টি আসন পায়। যদি পিআর পদ্ধতি থাকতো, আওয়ামী লীগ আনুপাতিকভাবে প্রায় ১৪৮টি আসন পেত এবং এককভাবে সরকার গঠন করতে পারতো না।
২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৪১% ভোট পেয়ে ১৯৩টি আসন জেতে, আর আওয়ামী লীগ ৪০% ভোট পেয়েও মাত্র ৬২টি আসন পায়। পিআর থাকলে বিএনপি ১২৩টি, আওয়ামী লীগ ১২০টি আসন পেত। ১৯৯১ সালে বিএনপি ৩১% ভোট পেয়ে ১৪০টি আসন পায়, আওয়ামী লীগ ৩০% ভোট পেয়েও মাত্র ৮৮টি আসন পায়। আনুপাতিক পদ্ধতিতে তখন বিএনপি ৯৩টি, আওয়ামী লীগ ৯০টি আসন পেত। এই বৈষম্যের ফলে সরকার গঠনের পরও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিবর্তে একদলীয় আধিপত্য কায়েম হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র দলীয়করণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, বিরোধী মত দমনের মতো প্রবণতা বেড়েছে। এর চরম রূপ দেখা গেছে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনকালে।
সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির সুবিধা:
পিআর পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটের মূল্য থাকে এবং সংসদে সব দলের প্রতিনিধি থাকার সুযোগ হয়। ছোট দলগুলোও জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। সংসদে কোনো বিল পাস করতে হলে অন্য দলের মতামত প্রয়োজন হবে, যা গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা বাড়াবে। এছাড়া নির্বাচনী সহিংসতা, সন্ত্রাস, কালো টাকার ব্যবহার ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব কমবে। এলাকার আধিপত্য বিস্তার, টেন্ডারবাজি, মনোনয়ন বাণিজ্য ও পরিবারতন্ত্র হ্রাস পাবে। সংসদ সদস্যরা এলাকা নয়, জাতীয় স্বার্থে আইন প্রণয়নে মনোযোগী হবেন। নারীদের সংরক্ষিত আসনের জন্য আলাদা নির্বাচনের প্রয়োজন থাকবে না এবং কোনো সাংসদের মৃত্যু বা পদত্যাগে উপনির্বাচনও লাগবে না। গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে এবং বহুদলীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
সমালোচনা ও মন্দ দিক:
তবে পিআর পদ্ধতিতে ভোটাররা সরাসরি প্রার্থী বেছে নিতে পারেন না। এলাকাভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরির সুযোগ কমে যায় এবং স্থানীয় সমস্যা উপেক্ষিত হতে পারে। দল কেন্দ্রীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ায় গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি ও মনোনয়ন বাণিজ্য বাড়তে পারে। এছাড়া সংখ্যালঘু কার্ড বা আবেগী স্লোগান ব্যবহার করে কিছু দল অল্প ভোটে সংসদে ঢুকে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এমনকি পরাজিত আওয়ামী ভাবধারার কোনো দলও পিআরের সুযোগ নিয়ে পুনরুত্থান করতে পারে। পিআর পদ্ধতির বিরোধীরা আরেকটি যুক্তি দেয় যে এতে ঝুলন্ত সংসদ হতে পারে, কিন্তু এফপিটিপি পদ্ধতিতেও ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের মতো ঝুলন্ত সংসদ হয়েছে।
নতুন বাস্তবতা:
২০২৬ সালের নির্বাচন নতুন প্রজন্মের জন্য প্রথম ভোটের অভিজ্ঞতা হবে। গত ১৭ বছরে প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়নি। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের স্মৃতি এবং ৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ভোটারদের মানসিকতায় গভীর প্রভাব ফেলবে। তাই পুরনো ভোটের শতাংশের হিসাব আগামী নির্বাচনে তেমন প্রভাব ফেলবে না। বড় দলগুলো পিআর পদ্ধতির বিরোধিতা করলেও এটা জাতীয় স্বার্থ ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন। সত্যিকারের বড় দল হলে পিআর পদ্ধতিতেও তারা বেশি আসনই পাবে। অন্যদিকে ছোট দলগুলো এতে সমর্থন দিচ্ছে, কারণ এতে তাদের সংসদে প্রবেশের সুযোগ বাড়বে।
সমাধান ও ভবিষ্যৎ:
১৯৯৫-৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যেমন রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছিল, তেমনি সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি নিয়েও সংঘাতের ঝুঁকি আছে। সমঝোতা না হলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। বড় দল যদি সত্যিই জনসমর্থনে আস্থাশীল হয়, তবে গণরায় মেনে নেওয়া উচিত।
১৯৯১ সালের গণভোটের মাধ্যমেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় আসে। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, এ দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারই বেশি কার্যকর হতে পারে, কারণ সাংবিধানিকভাবে আমরা সমজাতীয় (হোমোজেনাস) জনগোষ্ঠী। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। তবুও বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় পিআর পদ্ধতি অন্তত সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র ঠেকাতে বিকল্প সমাধান হতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে একমত হয়, তবে সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
লিখেছেন: জুবায়ের হাসান, রাজনৈতিক বিশ্লেষক
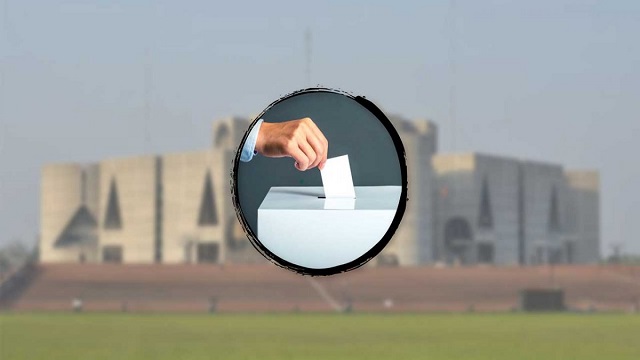
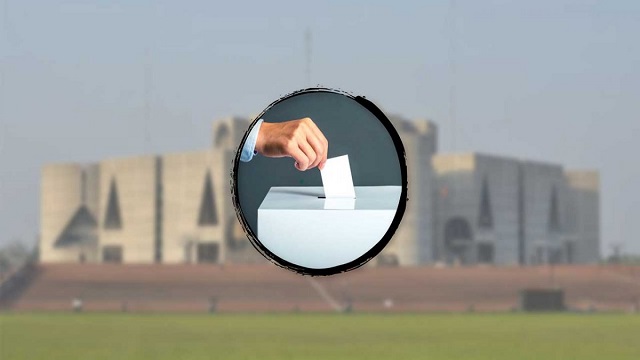
পাঠকের মন্তব্য
মন্তব্য পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত। এর জন্য সম্পাদক দায়ী নন।